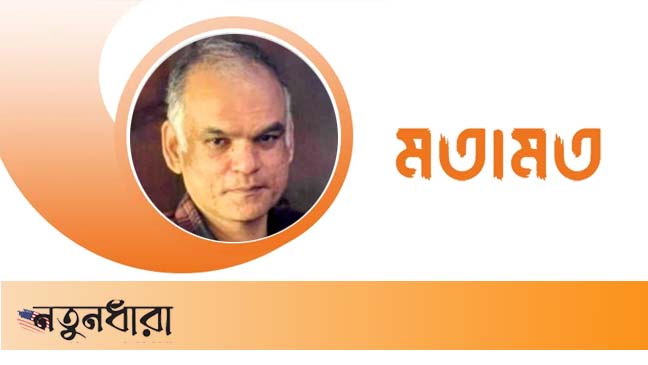
অন্তর্বর্তী সরকারকে ঘিরে বাংলাদেশের রাজনীতিতে বাড়ছে অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাস। এনসিপি ও ইসলামবাদী কিছু দলের সক্রিয়তা, এনজিও-সুশীল সমাজের প্রভাব এবং নির্বাচন নিয়ে জটিল হিসাব-নিকাশে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে অন্তর্বর্তী সরকারের অবস্থান।
প্রথমদিকে অন্তর্বর্তী সরকারকে নিজেদের সরকার বললেও দিন যতই গড়াতে থাকে, বিএনপি সরকারের সঙ্গে নিজেদের দূরত্ব তত বেশি অনুভব করা শুরু করে। বিএনপির নেতাকর্মীদের সামনে সরকারের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়।
সরকার কী চাচ্ছে, বা কোনদিকে দেশকে নিয়ে যেতে চায়, অথবা সরকারের স্বরূপ কী—এ বিষয়টগুলো শুরু থেকেই বিএনপিসহ অনেকের কাছেই পরিষ্কার নয়। ফলে, এ অবস্থায় তাদের করণীয় কী, এটা নিয়ে এক ধরণের সংশয় তৈরি হয়। লন্ডনে ইউনূস-তারেক বৈঠকের পর রাতারাতি এ দ্বিধা-সংশয় দূর হয়ে গেছে সেটা বলা যাবে না।
বিএনপি সমর্থক শহুরে মধ্য ও উচ্চবিত্তের একটা অংশ এনসিপির প্রতি সহানুভূতিশীল বলে মনে হচ্ছে। দলটির সমর্থকদের আরেকটি অংশ ইসলামবাদের লেন্স দিয়ে রাজনীতি ব্যাখ্যা করেন। ইসলামবাদী দলগুলোর প্রতি তাদের বিশেষ দুর্বলতা রয়েছে। অবশ্য সংখ্যার বিচারে বিএনপির সমর্থকদের মধ্যে তারা নগণ্য—যদিও অনেক সময় তাদের রাজনৈতিক ব্যাখ্যা দলের সাধারণ কর্মী সমর্থকদের ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করে।
আওয়ামী লীগ সরকার পতনের প্রথম দিকে বিএনপির ওপর মানুষের যে আস্থা পরিলক্ষিত হয়েছিল, গত ১০ মাসে তার অনেকটা নষ্ট হয়েছে মাঠপর্যায়ের নেতাকর্মীদের নানাবিধ অপরাধমূলক কার্যকলাপ, হাট-বাজার-ঘাট, ঘের, ব্যবসা-বাণিজ্যকেন্দ্র দখলসহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে পদ-পদবি বাগিয়ে নেওয়ার মতো নানান কিছুর ফলে। দলটির মাঝে স্বার্থকেন্দ্রিক উপদলীয় আন্তঃকোন্দল প্রবল—যেটা এমনকি বিভিন্ন জায়গায় প্রাণঘাতী সংঘাতে পর্যন্ত রূপ নিয়েছে।
বিএনপির চেইন অব কমান্ড ৫ অগাস্টের পর দুর্বল হয়েছে। ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষে মাঠ পর্যায়ের নেতা কর্মীদের নিয়ন্ত্রণে রাখা দুরূহ হয়ে উঠেছে। এমন একটি দলের পক্ষে কোন আন্দোলন গড়ে তোলা প্রায় অসম্ভব—বিএনপির বর্তমান অবস্থা জনমানসে এ বার্তাই দিচ্ছে।
বিএনপিসহ সমমনা দলগুলোর বিপরীতে এনসিপি তো বটেই, জামায়াতে ইসলামী এবং ইসলামবাদী আরও কোনো কোনো দল ও সংগঠন অধ্যাপক ইউনূসের সরকারকে নিজেদের সরকার মনে করে বলে রাজনৈতিক অঙ্গনে প্রতীয়মান। তাদের কর্মী, সমর্থকদের আচরণ, বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, বক্তব্য এবং সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এ সংক্রান্ত নানাবিধ পোস্টের কারণে জনমানসে এ ধারণা জন্মলাভ করেছে। এখন অবশ্য উল্টো হাওয়া বইতে শুরু করেছে, এই দল দুটি ইউনূসের বিরুদ্ধে বিএনপির প্রতি পক্ষপাতের অভিযোগ আনতে শুরু করেছে।
ইসলামবাদীদের উপলব্ধি হলো, বর্তমান সময়ে তারা যতটা মুক্ত পরিবেশে, স্বাধীনভাবে দলীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারছেন, সেটা স্বাধীন বাংলাদেশে এর পূর্বে কখনও সম্ভব হয়নি। তাদের কারো কারো আশঙ্কা, নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠিত হলে তাদের আজকের যে অবস্থান, সেটা ব্যাহত হতে পারে।
ইসলামবাদীদের সম্পর্কে জনমানসে এমন একটা ধারণা গড়ে উঠছে যে, তারা নির্বাচনকে কিছুটা প্রলম্বিত করতে চায়। নির্বাচন যত দেরিতে হবে, জনগণের সামনে বিএনপির ভাবমূর্তি ততই ক্ষুণ্ণ হবে, যেটা তাদেরকে আখেরে রাজনৈতিক সুবিধা দিবে–অনেক ইসলামবাদী এমনটাই মনে করেন। এমনটা নবগঠিত এনসিপির ভাবনা বলেও সাধারণ মানুষ মনে করেন।
ইসলামবাদীদের সম্মিলিত জনসমর্থনের তুলনায় এককভাবে দল হিসেবে বিএনপির জনসমর্থন অনেক বেশি; আর এটাই দলটির মূল শক্তি। সুষ্ঠু ভোট হলে এটি একটি বড় ফ্যাক্টর। কিন্তু রাজনীতির মাঠেই এটিই শেষ কথা নয়।
বর্তমান সরকারের সঙ্গে এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির (সুশীল সমাজ) একটা উল্লেখযোগ্য অংশ প্র্যতক্ষ এবং পরোক্ষভাবে যুক্ত আছেন। বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো সিভিল সোসাইটি এবং সরকার এভাবে একাকার হয়েছে—যেটা আগে কখনো ঘটেনি। সঙ্গে আছে এনসিপি এবং সমস্ত ইসলামবাদী দল ও গোষ্ঠী সমূহের সমর্থন।
রাজনৈতিক নেতৃত্বের ক্রমাগত দুর্বলতা এনজিও ও সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয়দের রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে নিয়ে এসেছে। পশ্চিমের আধুনিক উন্নত বিশ্বেও দেখা যাচ্ছে, টেকনো এলিটদের দ্বারা রাজনৈতিক নেতৃত্ব চ্যালেঞ্জের মুখে পড়ছেন—যাদের কোন কোন বিশ্লেষক টেকনো সামন্ত হিসেবে অভিহিত করেছেন। রাজনৈতিক নেতৃত্বকে হটিয়ে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার কেন্দ্রে আসতে চাচ্ছেন তারা। বাংলাদেশে এ জায়গাটা নিয়েছে এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির এলিটরা।
সত্তরের দশক থেকে বাংলাদেশে এনজিও বিকশিত হতে থাকে এবং ক্রমান্বয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে এনজিও আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় দেশে পরিণত হয়েছে। শুরু থেকেই বাংলাদেশের উন্নয়ন বিষয়ক নানা মডেল এনজিও এলিটরা হাজির করেছেন। বিভিন্ন সময়ে এ সংক্রান্ত নানা পরীক্ষা নিরীক্ষাও তারা করেছেন।
সত্তরের ও আশির দশকে তারা মনে করেছিলেন দেশকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে বামপন্থী দলগুলোর সঙ্গে মিত্রতা জরুরি। যার ফলে একটা দীর্ঘ সময় বাম দলগুলোর সঙ্গে কিছু এনজিওর মিত্রতা দেখা গেছে। তবে, ৯/১১পরবর্তী সময় থেকে তাদের এ উপলব্ধিতে পরিবর্তন আসে।
৯/১১ এর পর যুক্তরাষ্ট্র ‘সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধের’ যে নীতি নেয়, সেখানে ইসলামবাদীদের ভাল এবং মন্দ–এ দুভাবে চিহ্নিত করা হয়। যে সমস্ত ইসলামবাদী পশ্চিমের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে, সন্ত্রাসবাদের ওপর নির্ভর করে তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জন করতে চায় তাদের মন্দ ইসলামবাদী হিসেবে অভিহিত করা হয়।
অপরদিকে–যারা গণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনীতি এবং পশ্চিমের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলতে চায়–তারা ভালো ইসলামবাদী। লক্ষ্যণীয় যে, শুধু গণতান্ত্রিক পন্থা নয়, ভালো ইসলামবাদী হবার আরেকটি পূর্ব শর্ত–পশ্চিমের ভূরাজনৈতিক লক্ষ্য, উদ্দেশ্যসহ নানা বিষয়ে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা।
বাংলাদেশের এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির প্রায় পুরোটাই পশ্চিমের রাজনৈতিক চিন্তা, চেতনা, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ দ্বারা প্রভাবিত। তাই তাদের কাছে পশ্চিমের ‘ভালো’ এবং ‘মন্দ’ ইসলামবাদ তত্ত্বের আলোকে ভালো ইসলামবাদীদের সঙ্গে সহযোগিতা করবার নীতি যুক্তিযুক্ত মনে হয়।
এ সহযোগিতা জঙ্গিবাদ বা ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদ নির্মূল করবে। এভাবে জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর সদস্যদের মূলধারার রাজনীতিতে নিয়ে আসা সম্ভব হবে বলে তারা মনে করেন—যার মাধ্যমে দেশে ক্রমান্বয়ে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যাবে।
সব ধরনের ইসলামবাদীদের গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে নিয়ে আসতে পারলে খোদ ইসলামবাদের রাজনীতিরই মৌলিক পরিবর্তন ঘটবে। পশ্চিমা লিবারেল ধাঁচের গণতান্ত্রিক চর্চার মধ্যে ইসলামবাদীদের অভ্যস্ত করানো গেলে আখেরে সব ধরনের ‘ইসলামী বিপ্লবের’ আশঙ্কা দূর হবে।
এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির উল্লেখযোগ্য অংশ মনে করেন, শেখ হাসিনার অগণতান্ত্রিক স্বৈরশাসন বাংলাদেশে র্যাডিকাল ইসলামবাদের ক্ষেত্র তৈরি করেছে। তাই এ ধারার ইসলামবাদের বিকাশ রোধ করবার জন্য বহুত্ববাদের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক বাংলাদেশ গড়ে তোলা জরুরি। আর তার জন্য সর্বপ্রথম প্রয়োজন হাসিনার স্বৈরশাসনের–যেটাকে পপুলার টার্ম ব্যবহার করে ফ্যাসিবাদী শাসন বলা হয়—তার উচ্ছেদ।
এ শাসন উচ্ছেদ করবার জন্য সবচেয়ে সংগঠিত এবং নির্ভরযোগ্য রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে ইসলামবাদীদের বিবেচনায় নেওয়া হয়। এর মধ্য দিয়ে সেক্যুলার এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির সঙ্গে ইসলামবাদীদের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ক্ষেত্র তৈরি হয়।
এ বোঝাপড়া বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটিয়ে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ এবং রাষ্ট্র গঠন করবে—এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এমনটাই মনে করেন। বস্তুত এ বিবেচনা থেকেই এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির পাশাপাশি আওয়ামী লীগ বিরোধী সব ধরণের সেক্যুলার, প্রগতিশীল দাবিদার এবং বামপন্থীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ একটি কমন প্ল্যাটফর্মে অলিখিতভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়।
এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধিরা মূলত নিউ লিবারেল ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। তাদের কেউ কেউ নিউ লেফট ধারার অনুসারী। দুই পক্ষই রাষ্ট্র এবং সমাজে বহুত্ববাদিতার পক্ষপাতী। বহুত্ববাদিতাকে তারা গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি হিসেবে ধরেন।
বহুত্ববাদিতা হলো সমাজ এবং রাষ্ট্রে প্রায় সব ধরনের রাজনৈতিক এবং সামাজিক মতবাদ ও বিশ্বাসের সহাবস্থান। নারী-পুরুষের পাশাপাশি ট্রান্সজেন্ডার ও সমকামীদের সমান রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক অধিকার।
সমাজ বহুত্ববাদী না হলে রাষ্ট্রের পক্ষে বহুত্ববাদী হওয়া সম্ভব নয়। আর রাষ্ট্র বহুত্ববাদী না হলে সেটা গণতান্ত্রিক হবে না। এসব ভাবনা থেকেই সংবিধান সংস্কার কমিশন বহুত্ববাদিতার ধারণা পেশ করে। নারী বিষয়ক সংস্কার কমিশন নারী-পুরুষ সমনাধিকারসহ যৌন কর্মীদের অধিকার ও পেশার স্বাধীনতার বিষয় সামনে আনে।
এসব প্রস্তাব ইসলামবাদের রাজনীতির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রের তরফ থেকে তাত্ত্বিকভাবে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, যার মুখোমুখি এর পূর্বে তারা কখনও হয়নি। এসব প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে বাংলাদেশে ইসলামবাদের রাজনীতি বলে কিছু থাকে না। ফলে, ইসলামবাদীরা বহুত্ববাদিতা এবং নারী কমিশনের রিপোর্ট সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখান করে।
লক্ষ্যণীয় যে, বহুত্ববাদিতার কথা বলে আসা এনসিপিও ইসলামবাদীদের সঙ্গে সুর মিলিয়ে বহুত্ববাদিতা প্রত্যাখান করেছে। দেখা যাচ্ছে যে, এনজিও এবং সিভিল সোসাইটির প্রতিনিধি—যাদের কেউ কেউ নানাভাবে বর্তমানে শাসন কাঠামোর সঙ্গে যুক্ত—তাদের রাষ্ট্র ও সমাজ ভাবনার সঙ্গে এনসিপি ও ইসলামবাদীদের অবস্থান ভিন্ন এবং বিপরীতমুখি।
এ ভিন্ন এবং বিপরীতমুখি অবস্থার বাস্তবতাকে মাথায় রেখেই ফেব্রুয়ারির প্রথম দিকে নির্বাচনের সময় প্রাথমিকভাবে চিন্তা করা হয়েছে—যদিও সুনির্দিষ্ট দিন ক্ষণ এখনও ঘোষণা করা হয়নি। ফলে অনেকের মনে এখনো একটা সংশয় কাজ করছে এ ভেবে যে, ফেব্রুয়ারিতে আসলেই নির্বাচন হতে যাচ্ছে কিনা।
আবার নির্বাচন হলেও নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে কিনা সেটা একটা বড় প্রশ্ন হয়ে রয়েছে। নির্বাচনে যদি তাদের অংশগ্রহণ করতে দেওয়া না হয়, তাহলে একই সঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন চৌদ্দ দলীয় জোটের বাকি দলগুলোও নির্বাচনে অংশ নিতে পারবে না। আওয়ামী লীগকে সহযোগিতার সূত্র ধরে জাতীয় পার্টি, কিছু ইসলামবাদী দল এবং প্যাডসর্বস্ব আরো কিছু দলও এ নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে।
এতগুলো দলকে নির্বাচন প্রক্রিয়ার বাইরে রেখে নতুন সরকার গঠিত হলে, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারের প্রতিনিধিত্বশীলতার প্রশ্নকে ঘিরে রাজনীতিতে নতুন মাত্রা তৈরি হতে পারে। আবার, আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে দিলে এনসিপিসহ কিছু দল নির্বাচন বর্জন করতে পারে—যা রাজনীতিতে ভিন্ন সমীকরণ দাঁড় করাবে।
মানবিক বা ত্রাণ করিডোর, চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর দুবাইভিত্তিক কোম্পানিকে লিজ দেওয়া ইত্যাদি আরও কিছু বিষয় নিয়েও রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের মতদ্বৈধতা রয়েছে। প্রায় সব দলই মনে করে এসব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার এখতিয়ার একমাত্র নির্বাচিত সরকারের।
দেখা যাচ্ছে শুধু নির্বাচন নয়, নানা বিষয় ৫ অগাস্ট পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক সঙ্কট তৈরি করেছে। এ সঙ্কট থেকে উত্তরণে যেটি সবার আগে প্রয়োজন সেটি হলো জাতীয় এবং আন্তর্জাতিকভাবে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচন। অধ্যাপক ইউনূস নিজেই বলেছেন, তিনি বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে ভালো নির্বাচন দেশবাসীকে উপহার দিতে চান।
বাংলাদেশের ইতিহাসের এখন পর্যন্ত সবচেয়ে ভালো নির্বাচন হচ্ছে বিচারপতি সাহাবুদ্দিন আহমদের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচন, যা সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছিল।
অন্তর্বর্তী সকারের সামনে চ্যালেঞ্জ হল ১৯৯১-এর চেয়েও ভালো নির্বাচন করা। এ ধরনের নির্বাচনের মূল শর্ত—জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এর গ্রহণযোগ্যতা। এটা তখনই সম্ভব, যদি তাতে জনমতের প্রতিফলন থাকে।
একমাত্র জনমতের প্রতিফলনের ভিত্তিতে সরকার গঠিত হলেই ৫ অগাস্টের পর থেকে যে সঙ্কট তৈরি হয়েছে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে বাংলাদেশ। আর জনমতের সঠিক প্রতিফলনবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠিত হলে, সঙ্কট আরো গভীরতর হবে।
লেখক : গবেষক ও শিক্ষক, আমেরিকার পাবলিক ইউনিভার্সিটি
সূত্র: বিডি নিউজ