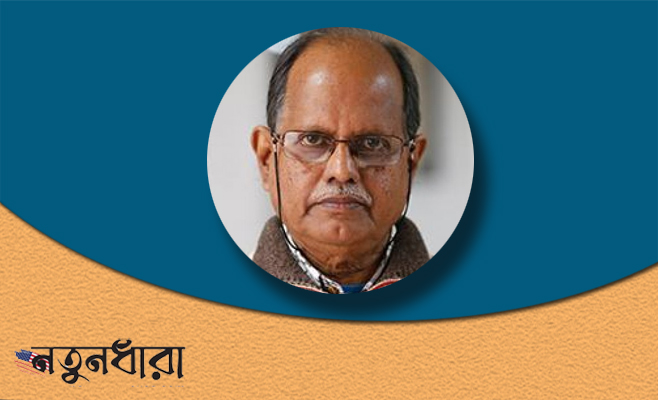
বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের মহত্তম চেতনায়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার পর স্বপ্ন দেখেছিলেন একটি গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক সমাজ গড়ার। কিন্তু সেই রাষ্ট্রপথ খুব বেশি দূর এগোতে পারেনি। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার মধ্য দিয়ে যে রাষ্ট্রীয় ষড়যন্ত্রের সূচনা হলো, সেটিই আসলে এই দেশে সহনশীলতা ও মানবিক রাজনীতির মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিলো। হত্যার পরপরই সংবিধান পরিবর্তন, মুক্তিযুদ্ধ বিরোধীদের পুনর্বাসন এবং সামরিক স্বৈরশাসনের উত্থান ঘটলো। এর ফলে রাজনীতির কেন্দ্রে চলে এলো প্রতিশোধ, ষড়যন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বীকে মুছে দেওয়ার প্রবণতা।
স্বাধীনতার পর প্রথম কয়েক বছরেই দেখা যায়, রাজনৈতিক অঙ্গনে মতবিরোধ থাকলেও বঙ্গবন্ধু বিরোধীদের সঙ্গে আলোচনার টেবিলে বসতেন, যুক্তি দিয়ে তাঁদের মোকাবিলা করতেন। কিন্তু তাঁর হত্যার পর নতুন শাসকেরা ভিন্নমতকে আর রাষ্ট্রের অংশ হিসেবে স্বীকার করলো না। শুরু হলো নিষিদ্ধকরণ, দমননীতি এবং দমনপীড়নের রাজনীতি। আওয়ামী লীগের কার্যক্রম স্থগিত করা হলো, অনেক নেতাকর্মীকে কারাগারে পাঠানো হলো, আবার মুক্তিযুদ্ধবিরোধী জামায়াত ও পাকিস্তানপন্থিদের রাজনীতিতে ফিরিয়ে আনা হলো। এই উল্টোপথে চলার ফলেই সমাজে সহনশীলতা ভেঙে পড়তে শুরু করলো।
অষ্টাদশ শতকের ইউরোপে গণতন্ত্র বিকাশের সময় বারবার বলা হয়েছিল—“I disapprove of what you say, but I will defend to the death your right to say it.” অর্থাৎ ভিন্নমতকে মেনে নেওয়া গণতন্ত্রের প্রাণ। কিন্তু বাংলাদেশে ১৯৭৫-এর পর রাজনীতির মূল সুর হয়ে দাঁড়াল— ‘তুমি ভিন্নমত পোষণ করছো, তাই তোমাকে নিশ্চিহ্ন করতে হবে।’ এই মানসিকতা ধীরে ধীরে সব রাজনৈতিক দলে ছড়িয়ে পড়লো।
সত্তর ও আশির দশকে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠলেও সেখানে গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির চর্চার সুযোগ কম ছিল। জিয়াউর রহমান থেকে শুরু করে এরশাদ পর্যন্ত শাসকেরা বিরোধীদের দমন করতে সেনা, পুলিশ, গোপন সংস্থা ব্যবহার করলেন। আন্দোলনের ভাষা হয়ে উঠলো হরতাল, বিক্ষোভ, লাঠি-পাল্টা লাঠি। বিরোধীকে ‘শত্রু’ ভাবা শুরু হলো। রাজনীতির যে ঐতিহ্য মুক্তিযুদ্ধের সময় গণসংহতির ওপর দাঁড়িয়েছিল, তা ক্রমে সরে গিয়ে দাঁড়ালো প্রতিশোধ আর প্রতিহিংসার ওপর।
নব্বইয়ের গণঅভ্যুত্থান এরশাদের পতন ঘটালেও সমাজে যে সহনশীল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কথা ছিল, তা হয়নি। বরং আওয়ামী লীগ ও বিএনপির দ্বন্দ্ব ক্রমশ শত্রুতার আকার নিলো। সংসদ বর্জন, নির্বাচন বর্জন, রাস্তা দখলের রাজনীতি—সবই প্রতিপক্ষকে ধ্বংস করার কৌশল হয়ে উঠলো। ক্ষমতায় আসার পর যে দলই রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, তারা চেষ্টা করেছে অন্য দলকে দুর্বল করে দিতে, দমন করতে। এভাবে প্রতিশোধের রাজনীতি সমাজে স্থায়ী হয়ে গেলো।
এই দীর্ঘ প্রেক্ষাপট বোঝা জরুরি, কারণ সম্প্রতি যে ঘটনা ঘটেছে—বঙ্গবন্ধু, শেখ হাসিনা, কিংবা শিল্পীদের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ—এটি কোনও হঠাৎ আবেগের বহিঃপ্রকাশ নয়। এটি মূলত সেই দীর্ঘদিনের প্রতিশোধপরায়ণ রাজনীতিরই প্রতিফলন, যা ১৯৭৫-এর পর থেকে প্রতিটি প্রজন্মকে শিক্ষা দিয়েছে: প্রতিপক্ষকে যুক্তি দিয়ে হারানো নয়, অপমান করে নিঃশেষ করতে হবে।
এভাবেই রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের ভেতরেও সহনশীলতার সংস্কৃতি ক্ষয়ে গেছে। ভিন্ন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকা মানেই শত্রুতা, কারও প্রতি শ্রদ্ধা জানানো মানেই ‘অন্য পক্ষের হয়ে যাওয়া’—এই মানসিকতা এখন প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে দাঁড়িয়েছে।
সংস্কৃতি অঙ্গনের দলীয়করণ ও প্রতিহিংসার বিস্তার
রাজনীতিতে প্রতিশোধের যে সংস্কৃতি ১৯৭৫-এর পর থেকে দৃশ্যমান হলো, তা শুধু সংসদীয় রাজনীতি বা ক্ষমতার লড়াইয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলো না। ধীরে ধীরে সেই প্রবণতা ঢুকে পড়লো আমাদের সংস্কৃতি অঙ্গনে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, ক্রীড়া জগতে—যেখানে আসলে থাকা উচিত ছিল মুক্তচিন্তার পরিসর, ভিন্নতার সৌন্দর্য এবং সৃজনশীলতার উন্মুক্ত বাতাস।
স্বাধীনতার পরপরই দেখা যায় শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীরা মূলত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের চেতনায় একত্রিত ছিলেন। তাঁদের সৃষ্টির মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছিল জাতীয়তাবোধ, অসাম্প্রদায়িকতা ও স্বাধীনতার স্বপ্ন। কিন্তু বঙ্গবন্ধু হত্যার পর সেই ধারার বিরুদ্ধেই কাজ শুরু হয়। মুক্তিযুদ্ধবিরোধীদের পুনর্বাসন করা হলো, সাহিত্য-সংস্কৃতির মঞ্চে মুক্তিযুদ্ধপন্থিদের কোণঠাসা করার চেষ্টা চললো। ৮০-এর দশকে যখন এরশাদের সামরিক শাসন চলছিল, তখনও শিল্পী-সাহিত্যিকরা আন্দোলনে নামেন, কিন্তু তাদের অনেকেই রাষ্ট্রীয় দমননীতি ও সেনা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতার শিকার হন।
সংস্কৃতি অঙ্গনের সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো—এটি হওয়া উচিত ছিল জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্র, কিন্তু তা পরিণত হলো বিভাজনের অঙ্গনে। যে শিল্পী বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানালেন, তিনি হঠাৎই ‘আওয়ামী শিল্পী’ হয়ে গেলেন। যিনি শেখ হাসিনার সমালোচনা করলেন, তিনি ‘বিএনপি বা বিরোধী পক্ষের লোক’ বলে চিহ্নিত হলেন। এভাবে ব্যক্তির শিল্প বা সৃজনশীলতা নয়, বরং তার রাজনৈতিক মত বা ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টকে মাপকাঠি করা হলো।
গণতন্ত্র ফেরার পর প্রত্যাশা ছিল যে সংস্কৃতি অঙ্গন দলীয় প্রভাব থেকে মুক্ত হবে। কিন্তু হলো উল্টো। আওয়ামী লীগ বা বিএনপি—দুই দলই সংস্কৃতি ক্ষেত্রকে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের জায়গা বানালো। শিল্পী সমিতি, লেখক সংঘ, সাংবাদিক ইউনিয়ন—সবখানে দ্বন্দ্ব তৈরি হলো দলীয় আনুগত্যের ভিত্তিতে। কে আওয়ামী ঘরানার, কে বিএনপি ঘরানার—এই মাপকাঠিতে শিল্পীর প্রতিভা বা লেখকের কলমকে বিচার করা শুরু হলো।
ক্রীড়া জগৎ বাদ গেলো না। ক্রিকেট বোর্ড, ফুটবল ফেডারেশন, বিভিন্ন ক্রীড়া সংগঠন—সবখানেই রাজনৈতিক পরিচয় প্রধান হয়ে উঠলো। যে দল ক্ষমতায় আসলো, তাদের ঘনিষ্ঠ ক্রীড়া সংগঠক বা ব্যবসায়ীই বোর্ডের কর্তৃত্ব নিলো। ফলে ক্রীড়ার মাপকাঠি হয়ে গেলো দক্ষতা নয়, বরং দলীয় ঘনিষ্ঠতা। এই প্রক্রিয়া সাকিব আল হাসান বা অন্য তারকাদেরও মাঝে মাঝে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেছে।
সংস্কৃতি অঙ্গনের সবচেয়ে দুঃখজনক দিক হলো—এটি হওয়া উচিত ছিল জাতীয় ঐক্যের ক্ষেত্র, কিন্তু তা পরিণত হলো বিভাজনের অঙ্গনে। যে শিল্পী বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানালেন, তিনি হঠাৎই ‘আওয়ামী শিল্পী’ হয়ে গেলেন। যিনি শেখ হাসিনার সমালোচনা করলেন, তিনি ‘বিএনপি বা বিরোধী পক্ষের লোক’ বলে চিহ্নিত হলেন। এভাবে ব্যক্তির শিল্প বা সৃজনশীলতা নয়, বরং তার রাজনৈতিক মত বা ব্যক্তিগত ফেসবুক পোস্টকে মাপকাঠি করা হলো।
ফলে সমাজে ভয়ের পরিবেশ তৈরি হলো। অনেকে আর খোলাখুলি মত দিতে চাইছেন না, কারণ জানেন, সামান্য শ্রদ্ধা প্রদর্শনও কালকে তাদের ছবি জুতাপেটার ব্যানারে উঠিয়ে দিতে পারে। এই ভয়ই আসলে আমাদের সংস্কৃতিকে মেরে ফেলছে।
যেটি হলো—বঙ্গবন্ধু ও শেখ হাসিনার পাশাপাশি সাকিব আল হাসান, জয়া আহসান, শম্পা রেজা, শাকিব খানের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ—এটি সেই দীর্ঘ প্রক্রিয়ারই বহিঃপ্রকাশ। রাজনীতির প্রতিহিংসা এখন শিল্প-সংস্কৃতির শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করছে। অথচ এরা সবাই মূলত শিল্পের মানুষ, যাদের কাজ মানুষকে একত্র করে, সৌন্দর্যের দিকে টানে। কিন্তু তাদেরও টেনে নামানো হচ্ছে প্রতিশোধের কাদায়।
এভাবে সংস্কৃতি অঙ্গনের দলীয়করণ শুধু শিল্পী-লেখকদের ক্ষতি করছে না; এটি ধীরে ধীরে গোটা সমাজের রুচি ও মানবিকতাকেও বিনষ্ট করছে। কারণ সমাজ যদি শিল্পীকে শিল্পী হিসেবে না দেখে, কেবল দলীয় পরিচয়ে দেখে, তবে সেই সমাজে সৃজনশীলতার জায়গা আর থাকে না। তখন কেবল টিকে থাকে ঘৃণা, বিভক্তি আর প্রতিহিংসা। এটি হলো সেই দীর্ঘ রাজনৈতিক প্রতিহিংসার চর্চার পরিণতি, যার শেকড় গভীরভাবে প্রোথিত হয়েছে আমাদের সমাজে।
ঘটনাটি ঘটেছে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকীর দিন, ১৫ আগস্টের প্রেক্ষাপটে। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া একজন রাষ্ট্রনেতাকে স্মরণ করা— এটি একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার। বিশ্বের যেকোনও দেশে প্রতিষ্ঠাতা নেতা বা জাতীয় বীরকে স্মরণ করা হয় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিকভাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জর্জ ওয়াশিংটন, ভারতে মহাত্মা গান্ধী কিংবা দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলা—তাঁদের মৃত্যুবার্ষিকী বা জন্মদিনে শ্রদ্ধা জানানো নিয়ে কখনও বিতর্ক হয় না। কিন্তু বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুকে ঘিরে পরিস্থিতি একেবারেই ভিন্ন। এখানে তাঁকে স্মরণ করলেই তা হয়ে যায় রাজনৈতিক বিভাজনের সূচনা।
কেউ যদি বঙ্গবন্ধুকে শ্রদ্ধা জানায়, তবে তাঁকে ‘শত্রু পক্ষের’ বলে গণ্য করা হচ্ছে। আবার কেউ যদি শেখ হাসিনার সমালোচনা করে, তবে তাকেও একশ্রেণি সহজেই ‘রাষ্ট্রবিরোধী’ বা ‘ষড়যন্ত্রকারী’ আখ্যা দেয়। অর্থাৎ দুইপক্ষই প্রতিপক্ষকে মানসিক ও সামাজিকভাবে ধ্বংস করতে চায়।
ফলে যে সমাজে মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু, কিংবা গণতন্ত্রের চেতনা নিয়ে গর্ব করার কথা, সেই সমাজেই আজ দেখা যাচ্ছে এই বিষয়গুলো ঘৃণা ও বিদ্বেষের উৎসে পরিণত হয়েছে। ইতিহাসকে নিরপেক্ষভাবে দেখা যাচ্ছে না। কারও কাছে বঙ্গবন্ধু কেবল আওয়ামী লীগের প্রতীক, কারও কাছে আবার তাঁর নাম উচ্চারণ করাও অপরাধ। কিন্তু সত্য হলো—তিনি বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা, যাঁকে স্মরণ করা রাষ্ট্র ও সমাজেরই দায়িত্ব। তাঁর অবদান নিয়ে বিতর্ক হতে পারে, সমালোচনা হতে পারে, কিন্তু তাঁকে স্মরণ করাকে অপরাধে পরিণত করা কেবল অসহিষ্ণুতারই বহিঃপ্রকাশ।
এই পরিস্থিতি আমাদের সামনে দুটি বড় সংকেত দিচ্ছে।
প্রথমত, রাজনীতিতে সহনশীলতার জায়গা প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে গেছে। এখন কারও মত প্রকাশ মানেই ‘আমার শত্রু’—এই ধারণাই আধিপত্য করছে।
দ্বিতীয়ত, শিল্প-সংস্কৃতি বা শিক্ষাক্ষেত্রও সেই একই বিভাজনে নিমজ্জিত হচ্ছে, যা সমাজকে আরও অস্থির করছে।
এই ঘটনাটি আসলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল—আমরা কেবল প্রতিপক্ষকে নষ্ট করার রাজনীতি শিখেছি, সহাবস্থানের রাজনীতি শিখিনি।
তরুণ প্রজন্মের বড় চ্যালেঞ্জ
১. সহনশীলতার অভাব:
তরুণরা আজকের সমাজে দেখছে—শ্রদ্ধা, স্মরণ বা সমালোচনা—কোনও কিছুকেই জায়গা দেওয়া হচ্ছে না। এর ফলে তারা ধারণা করছে ভিন্নমত মানেই শত্রুতা।
২. ইতিহাসের বিভাজন:
কেউ শেখ মুজিবকে শুধু আওয়ামী লীগের প্রতীক মনে করছে, কেউ তাঁকে পুরোপুরি অস্বীকার করছে। তরুণরা সঠিক ইতিহাস জানার পরিবর্তে বিভক্ত ইতিহাস পাচ্ছে, যা তাদের মননকেও বিভাজিত করছে।
৩. সংস্কৃতির সংকীর্ণতা:
শিল্প, সাহিত্য, সংগীত, ক্রীড়া—এসবকে আনন্দ বা ঐক্যের উৎস হিসেবে দেখার বদলে তরুণরা এগুলোকে রাজনৈতিক লড়াইয়ের অংশ হিসেবে দেখতে শিখছে।
করণীয় কী?
প্রথমত, আমাদের মনে রাখতে হবে বিতর্ক, সমালোচনা ও মতভেদ- এগুলোই গণতন্ত্রের সৌন্দর্য। বঙ্গবন্ধুকে স্মরণ মানে আওয়ামী লীগকে অন্ধভাবে সমর্থন নয়; একইভাবে শেখ হাসিনার সমালোচনা মানে রাষ্ট্রবিরোধিতা নয়। তরুণদের এই মৌলিক সত্যগুলো শিখতে ও শেখাতে হবে।
দ্বিতীয়ত, শিল্প-সংস্কৃতি ও খেলাধুলাকে দলীয়করণ থেকে মুক্ত করতে হবে। একজন শিল্পী যদি গান করেন, নাটক করেন বা চলচ্চিত্র বানান, তাঁকে কেবল শিল্পী হিসেবেই দেখা উচিত, রাজনৈতিক লেবেল টাঙিয়ে নয়।
তৃতীয়ত, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে যুক্তি দিয়ে বিতর্ক শেখানো দরকার, অপমান দিয়ে নয়। ছাত্রসমাজই যদি জুতা নিক্ষেপকে প্রতিবাদের ভাষা মনে করে, তবে ভবিষ্যতে তারা কেবল ঘৃণাই চর্চা করবে। তাই বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজগুলোতে সহনশীলতা, সমঝোতা ও যুক্তিনির্ভর আলোচনার পরিবেশ তৈরি করা অপরিহার্য।
চতুর্থত, তরুণদের ইতিহাস জানাতে হবে পূর্ণাঙ্গভাবে। শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার ইতিহাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র—এটি যেমন সত্য, তেমনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনের নানা বিতর্ক বা সমালোচনাও আলোচনায় আসতে পারে। কিন্তু সেগুলো আলোচনার মাধ্যমে হতে হবে, অপমান বা বিকৃতির মাধ্যমে নয়।
তরুণ প্রজন্ম যদি ঘৃণা নয়, সহনশীলতা বেছে নেয়—তবে ভবিষ্যতের বাংলাদেশ হবে একটি সভ্য, যুক্তিনির্ভর ও মানবিক সমাজ। আর যদি তারা আজকের মতো প্রতিপক্ষকে অপমান করার রাজনীতিই চালিয়ে যায়—তাহলে আমরা আরও বেশি বিভক্ত, আরও বেশি ক্ষতবিক্ষত এক সমাজের দিকে এগিয়ে যাব।
ভবিষ্যৎ তাই তরুণদের হাতেই। তারাই ঠিক করবে—ঘৃণার রাজনীতি টিকিয়ে রাখবে, নাকি শ্রদ্ধা ও সহাবস্থানের নতুন সংস্কৃতি গড়ে তুলবে।
লেখক: সিনিয়র সাংবাদিক
সূত্র: বাংলা ট্রিবিউন