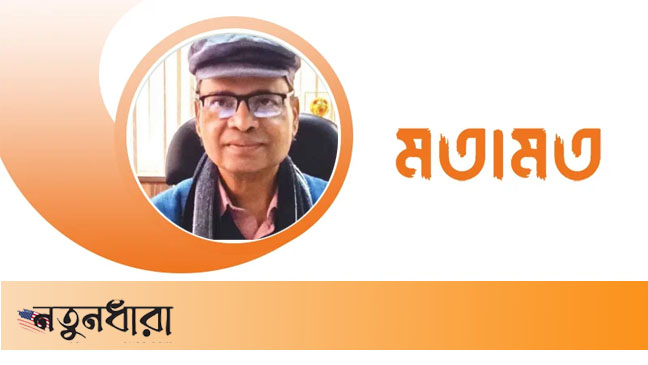
স্বাধীনতার ৫৩ বছর গত হতে চলেছে। আমাদের মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম লক্ষ্য ছিল গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভোটাধিকারের মাধ্যমে সরকার গঠন এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণ করা। ১৯৭০ সালে আওয়ামী লীগের নির্বাচনি প্রচারাভিযান চলাকালে ‘সোনার বাংলা শ্মশান কেন?’ শীর্ষক একটি প্রচার পত্রে তত্কালীন পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য তুলে ধরা হয়েছিল।সেই নির্বাচনি পোস্টার জনমত গঠনে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই দেশের মানুষ গণতান্ত্রিক এবং অর্থনৈতিক বৈষম্যহীন একটি সমাজব্যবস্থা প্রত্যাশা করেছিল। কিন্তু দীর্ঘ দিনেও সেই প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। বরং দিনকে দিন অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য শুধু বেড়েই চলেছে।
বৈষম্যের অনেক ধরন আছে। এর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিকসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে বৈষম্য যেমন বিভিন্ন মাত্রায় আছে, তেমনি আবার শ্রেণিতে শ্রেণিতে ঘনীভূত বৈষম্যও আছে। নারী পুরুষে বৈষম্য আছে। বর্ণে বর্ণে বৈষম্য আছে। সাধারণভাবে এই বৈষম্যকে আমরা বাহ্যিক বৈষম্য বলতে পারি। আবার একই গ্রুপের মধ্যেও বৈষম্য আছে। যেমন শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে যারা মানসিক শ্রমজীবী এবং যারা শারীরিক শ্রমজীবী তাদের মধ্যেও বৈষম্য বা অসমতা রয়েছে। যারা মানসিক শ্রমজীবী তারা শারীরিক শ্রমজীবীদের তুলনায় বেশি মজুরি পেয়ে থাকেন। নারীদের মধ্যেও যারা শিক্ষিত ও কর্মজীবী তাদের স্বাধীনতা অন্য নারীদের তুলনায় বেশি।
মানসিক এবং শারীরিক শ্রমজীবীরা কেউই পরস্পর শোষক নন। তারা উভয় শ্রেণিই নিয়োগকারী কর্তৃক শোষিত হয়ে থাকেন। একজন শ্রমজীবী বেঁচে থাকার জন্য যে মজুরি/বেতন পাওয়া উচিত তা তাদের দেওয়া হয় না। নানা অজুহাতে শ্রমজীবীদের ন্যায্যমজুরি প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করা হয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় এটা ধরে নেওয়া হয় যে, যারা মানসিক শ্রমজীবী তারা শারীরিক শ্রমজীবীদের তুলনায় বেশি মজুরি পাবেন। সে ক্ষেত্রে শ্রমের ঘনত্ব ও পূর্বে নিয়োজিত শ্রম তথা লেখাপড়ার জন্য নিয়োজিত শ্রমকে বিবেচনায় নেওয়া হয়।
কিন্তু একচেটিয়া বা ক্রমবধ্যমান পুঁজিপতির সঙ্গে শ্রমিকের যে বৈষম্য সেটা হয় উপর্যুপরি শোষণের কারণে। সেটাই হয়ে যায় স্থায়ী শ্রেণিবৈষম্য। বংশানুক্রমিক মজুরি দাসত্বই এর চূড়ান্ত পরিণতি। পুঁজিপতিদের মধ্যে চালাক যারা তারা সংস্কারের মাধ্যমে একে সহনীয় বা মানবিক করতে চাইলেও, কাঠামোগত কারণে তা কম সময়েই সফল হয়। এসব সংস্কার প্রায় সময়ই শ্রমিকদের বিপুল সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে হয়।
একজন শ্রমিকের সঙ্গে অন্যজন শ্রমিকের যে বৈষম্য সেটা অভ্যন্তরীণ সীমিত বৈষম্য। পুঁজিপতিদের মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান। ছোট পুঁজিপতি, মাঝারি পুঁজিপতি এবং বড় পুঁজিপতি আছে। আবার একচেটিয়া পুঁজিপতি আছে। একইভাবে বহুজাতিক পুঁজিপতি আছে। এদরে মধ্যেও বৈষম্য বিদ্যমান রয়েছে। অর্থাত্ পুঁজিপতি হলেই যে তারা বৈষম্যহীন পরিবেশে বাস করবেন, তা নয়।
আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যের বিষয়টি সহজ মনে হলেও ধারণাটি অত্যন্ত জটিল। বৈষম্যের ধারণাটি বিচার করার জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কার সঙ্গে কার বৈষম্য। আর অন্যটি হচ্ছে কোন বিষয়ে বৈষম্য। আমরা যখন বিষয়গতভাবে বৈষম্য পরিমাপ করি তখন অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি।
আপাতদৃষ্টিতে বৈষম্যের বিষয়টি সহজ মনে হলেও ধারণাটি অত্যন্ত জটিল। বৈষম্যের ধারণাটি বিচার করার জন্য দুটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে একটি হচ্ছে কার সঙ্গে কার বৈষম্য। আর অন্যটি হচ্ছে কোন বিষয়ে বৈষম্য। আমরা যখন বিষয়গতভাবে বৈষম্য পরিমাপ করি তখন অর্থনৈতিক বৈষম্য, সামাজিক বৈষম্য, সাংস্কৃতিক বৈষম্য, রাজনৈতিক বৈষম্য ইত্যাদি বিষয়গুলোকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকি। এসব বৈষম্য পরিমাপ করার সময় কিছু ইন্ডিকেটর বা সূচক ব্যবহার করা হয়। অর্থনৈতিক বৈষম্য পরিমাপ করার সময় আয় এবং সম্পদের বৈষম্যকে বিবেচনায় নিয়ে থাকি।
আমরা তখন পুরো সমাজকে দুটো ভাগে বিভক্ত করে আয় এবং সম্পদের বৈষম্য কতটুকু তা বিবেচনা করে থাকি। সম্পদ এবং আয় বণ্টনের ক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হলো—সম্পদ অর্জনের ক্ষেত্রে কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করা হয়েছে কি না। আয়ের বৈষম্য যদি শ্রমিকের দক্ষতার কারণে হয় তাহলে সেটাকে আমরা প্রায়ই যৌক্তিক বৈষম্য বলে মনে করে থাকি। কারণ দক্ষ শ্রমিক এবং অদক্ষ শ্রমিককে যদি একই পরিমাণ মজুরি দেওয়া হয় তাহলে সেটা দক্ষ শ্রমিকের প্রতি অবিচার করা হবে। কিন্তু যদি দেখা যায়, একই ধরনের কাজ করছেন তাদের মধ্যে একজন নারী এবং একজন পুরুষ নারী শ্রমিকের তুলনায় বেশি মজুরি পাচ্ছেন তাহলে সেটা নিখাদ বৈষম্য হিসেবেই বিবেচিত হবে। বৈষম্য বিচারের সময় গ্রুপের অভ্যন্তরীণ এবং গ্রুপে গ্রুপে বাহ্যিক বৈষম্য যেমন বিবেচনায় নিতে হয় তেমনি বৈষম্য সৃষ্টির প্রক্রিয়াকেও বিচার করতে হয়।
এই তাত্ত্বিক কাঠামো দিয়ে যদি বাংলাদেশের বৈষম্যকে বিশ্লেষণ করি তাহলে অনুধাবন করা যাবে বাংলাদেশে বৈষম্য কেন বাড়ছে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে এবং কাদের সঙ্গে বৈষম্য বাড়ছে—তা নির্ণয় করা যাবে। তেমনি বৈষম্যের কারণও বোঝা যাবে। প্রথমেই দেখা যাক, বাংলাদেশে কোন ক্ষেত্রে বৈষম্যটা বাড়ছে বলে আমরা মনে করছি। বাংলাদেশে বিভিন্ন ক্ষেত্রেই বৈষম্য বাড়ছে, তবে আয়ের বৈষম্যটাই সবচেয়ে বেশি এবং দৃষ্টিকটুভাবে বাড়ছে। আয়বৈষম্য যদি বিবেচনায় নেওয়া হয় তাহলে দেখা যাবে, বাংলাদেশে যারা সবচেয়ে বেশি অর্থ উপার্জন করে তারা মোট জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ। নিচের দিকে ৫০ শতাংশ মানুষের আয় বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, এদের আয় ক্রমশ সামাজিক মানদণ্ডে হ্রাস পাচ্ছে। আর সমাজের ওপরের শ্রেণিতে থাকা ১ শতাংশ মানুষের আয় যে দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে, নিচের দিকে তা ততটা দ্রুত গতিতে বাড়ছে না। আর যারা বেকার বা অক্ষম বা সুযোগবঞ্চিত তাদের আয় আসলে কমছে!
রাষ্ট্রের অর্জিত কর আয়ের বড় অংশই এই ১ শতাংশ মানুষের সুবিধার জন্যই ব্যয়িত হয় বা তারা কোনো না কোনোভাবে তা তাদের ভান্ডারে নিয়ে জমা করেন। বাংলাদেশে যে বৈষম্য বাড়ছে তা আমরা জানতে পারি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ‘হাউজ হোল্ড ইনকাম অ্যান্ড এক্সপেনডিচার’ সার্ভে থেকে। এটা শুরু হয়েছিল ১৯৭৭ সালে। এর পর থেকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর এই পরিসংখ্যান প্রকাশ করা হচ্ছে। পারিবারিক আয় এবং ব্যয়ের ভিত্তিতে এই হিসাবটি করা হয়। আয় বৈষম্যকে আবার আঙ্কিক পদ্ধতিতে পরিমাপ করা হয়। তার নাম হলো গিনি সহগ। গিনি ইনডেক্স দিয়ে যখন বৈষম্য পরিমাপ করা হয় শহরের আয়-ব্যয়ের বৈষম্য এবং গ্রামের আয়-ব্যয়ের বৈষম্য আলাদাভাবে বের করা যায়। গিনি সহগ মোতাবেক বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে যেমন আয় বৈষম্য বাড়ছে তেমনি শহরেও বাড়ছে।
সাধারণভাবে মনে করা হয় গিনি ইনডেক্স যদি দশমিক ৫০-এর ওপরে চলে যায় তাহলে সেই দেশের আয় বৈষম্য বিপজ্জনক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে বলে মনে করা হয়। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে স্বল্পোন্নত দেশ, মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে কোনো দেশকে চিহ্নিত করা হয়। মাথাপিছু গড় জাতীয় আয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ এখন মাঝারি আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে। মাঝারি আয়ের দেশে পরিণত হয়েছে এমন অনেক দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য কোনো কোনো সময় বেশি থাকে কখনো কমও থাকে (০.২০ থেকে ০.৫৬ পর্যন্ত)। পুঁজিবাদী বিশ্বে বৈষম্য থাকবেই এমন একটি ধারণা মেনে নেওয়া হয়। ইদানীং পুঁজিবাদী দেশের অর্থনীতিবিদগণও মনে করেন, কোনো দেশে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পেলে গণতন্ত্র টিকতে পারে না। এই অবস্থায় স্বৈরাচার বা একনায়কতন্ত্র মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। এই অবস্থায় সামন্তবাদ ধ্বংস করে গণতন্ত্র কায়েম করেছি পুঁজিবাদীদের সেই দাবি আর ধোপে টেকে না।
মূলত এ কারণেই পুঁজিবাদী দেশগুলো সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করে। রুজভেল্ট প্রথম ‘New Deal’-এর মাধ্যমে এই উদ্যোগ গ্রহণ করে। এ ধরনের সংস্কারমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থাকে পরবর্তীকালে কল্যাণ রাষ্ট্র বলা হয়। কল্যাণ রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষের জীবন মান উন্নয়ন এবং বৈষম্য কমানোর জন্য রাষ্ট্র নানাভাবে উদ্যোগ নিয়ে থাকে। কিন্তু সবাই তো পলিটিক্যালি কল্যাণ রাষ্ট্র নয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো যেখানে মধ্যম শ্রেণির ক্ষমতা বেশি এবং সার্বজনীন শিক্ষা আছে সেখানে হলো কল্যাণ রাষ্ট্র। আপনি যদি গিনি ইনডেক্স দিয়ে বিচার করেন তাহলে দেখবেন ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোতে গিনি ইনডেক্স অনেক কম। হয়তো দশমিক ২০ বা তারও নিচে। কোনো কোনো দেশ আছে যেখানে গিনি ইনডেক্স খুবই বেশি। যেমন ব্রাজিল, দক্ষিণ আফ্রিকা, চীন ইত্যাদি। বাংলাদেশও বর্তমানে সেই কাতারেই পড়বে।
অর্থনৈতিক বৈষম্য যদি ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পায় তাহলে একটি দেশে গণবিপ্লব বা গণবিস্ফোরণ ঘটাতে পারে। চীনে অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যাপক মাত্রায় বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেখানে গণবিপ্লব বা গণবিস্ফোরণ হয়নি, তার কারণ হচ্ছে চীনে আয়ের বৈষম্যটাকে অন্য কতগুলো পলিসি দিয়ে কাউন্টার অ্যাক্ট করা হয়। এসব পলিসি ধনতান্ত্রিক কল্যাণ রাষ্ট্রের গৃহীত নীতির অনেকটা অনুরূপ। যেমন চীন শিক্ষাব্যবস্থাকে সর্বজনীন অধিকারে পরিণত করেছে। স্বাস্থ্যসেবাকে সবার জন্য নিশ্চিত করেছে। যে কোনো মানুষ যদি বেকার থাকে রাষ্ট্র তাকে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করে।
আইন করে ন্যূনতম মজুরি নিশ্চিত করা হয়েছে। আগে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির একদলীয় শাসন ছিল। দুর্নীতি ও আমলাতন্ত্র ছিল। এখন কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরে বহুমতের গণতন্ত্র চর্চার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে প্রতিটি প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বেড়েছে। রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থেকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে কোনো দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে না। চীনের এই মডেলকে অনেকেই বাজার সমাজতন্ত্র বা শঙ্কর বা মিশ্র মডেল বলে থাকেন। সেখানে রাষ্ট্রের শক্তিশালী হস্তক্ষেপ যেমন আছে তেমনি বাজার প্রতিযোগিতাও আছে।
বর্তমানে পুঁজিবাদী পণ্ডিতরা নিউ লিবারাল ভাবাদশেও প্রচার করে থাকেন। নিউ লিবারেল রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বৈষম্য কমানোর তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই। সবচেয়ে জঘন্য রাষ্ট্র হচ্ছে সেগুলো যেগুলো নিউ লিবারেল ইকোনমি দিয়ে শুরু হয়েছে কিন্তু পরবর্তীকালে ক্রনি ক্যাপিটালিজমে পরিণত হয়েছে। নিউ লিবারেল ইকোনমিতে যেটা হয় তাহলো বিত্তবান শ্রেণির মানুষ আরো অর্থবিত্তের মালিক হতে থাকে।
আর গিনি সহগ আরো বাড়তে থাকে। আয় বৈষম্য বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যখন অর্থনীতিতে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সৃষ্টি হয়। একসময় সেই একচেটিয়া পুঁজিবাদ দক্ষ পুঁজিবাদ থাকে না, প্রতিযোগিতামূলক তো নয়ই। নিউ লিবারেল অর্থনীতি যখন প্রতিযোগিতাকে সম্পূর্ণ অবাধ এবং রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপকে বাতিল করে দেওয়ার কথা বলে কার্যত সংকীর্ণ অলিগার্কির মধ্যে প্রতিযোগিতা সীমাবদ্ধ করে ফেলে। তখন একচেটিয়া পুঁজি গঠন, মধ্যস্বত্বভোগীদের দাপট এবং অলিগার্কিও সংকীর্ণ চক্র তৈরি হয়। কোনো সমাজে অলিগার্কি সৃষ্টি হলে তারা সম্পদের বলে বলীয়ান হয়ে রাজনীতি এবং রাষ্ট্র ক্ষমতাকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। তারা রাষ্ট্র যন্ত্রকে যেমন নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তেমনি আমলাতন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।
অলিগার্কির একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তারা সর্বত্র তাদের প্রভাব বিস্তার করে এবং বিভিন্ন স্থানে তাদের নিজেদের আত্মীয়স্বজন অথবা পছন্দের লোকদের নিয়োগ করতে সক্ষম হয়। যারা কতিপয় মানুষের আনুকূল্যে বিভিন্ন স্থানে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় তারা নিয়োগকর্তাদের চাহিদা পূরণে সদা ব্যস্ত থাকেন। অসত্ রাজনীতিবিদ, অসত্ আমলা এবং অসত্ ব্যবসায়ীদের একটি শক্তিশালী চক্র গড়ে ওঠে। এরাই মূলত অর্থনীতিসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এই চক্রটিকেই পরবর্তী সময়ে অলিগার্কি নাম দেওয়া হয়। বাংলাদেশের বিষয়টি হচ্ছে সেই ধরনের। এখানে অসত্ আমলা, অসত্ ব্যবসায়ী এবং অসত্ রাজনীতিবিদের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী চক্র গড়ে উঠেছে, যারা রাষ্ট্রযন্ত্র থেকে শুরু করে সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছে।
১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে সেই সময় অলিগার্কি ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময় অলিগার্কি ভেঙে দেওয়া কঠিন হয়নি। কারণ এই অলিগার্কি গড়ে উঠেছিল বিজাতীয় ২২ পরিবারের সমন্বয়ে। এদের মধ্যে ২১টি পরিবারই ছিল অবাঙালি, অর্থাত্ পাকিস্তানি। তখনো বাংলাদেশিদের সমন্বয়ে অলিগার্কি তৈরি হয়নি। এমনকি বাংলাদেশি বৃহত্ পরিবারগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা পাটকল, বস্ত্রকলগুলোও রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়। স্বাধীনতার প্রেরণা বা চেতনা ছিল বৈষম্য কমানো। জাতীয়করণকৃত কারখানাগুলো প্রতিশ্রুতি ছিল এখানে মুনাফা সৃষ্টি হবে, দক্ষতা তৈরি হবে।
শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। তাদের সন্তানরা শিক্ষা, স্বাস্থ্য, চিকিত্সার সুযোগ পাবে। কিন্তু জাতীয়করণ করার পর অসচেতন শ্রমিকরা ভাবতে শুরু করে বা তাদের ভাবানো হয় আমরা প্রতিষ্ঠানের মালিক হয়ে গেছি। কাজেই কাজ না করলেও চলবে। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানে দুর্নীতি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ফলে একসময়ের লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো লোকসানি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হতে শুরু করে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বামপন্থি শ্রমিকদের বিতাড়িত করা হলো। শুরু হলো আওয়ামী লীগের তদানীন্তন সাদু-রায়হান পরিচালিত শ্রমিক লীগ নেতৃত্বে পরিচালিত লুটপাটতন্ত্র।
রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের এই অনিয়ম-দুর্নীতি রোধে তত্কালীন আওয়ামী লীগ সরকার কোনো কঠোর ব্যবস্থা নেননি। বামপন্থি শ্রমিকরা (বাওয়ানীর শহীদুল্লাহ্ চৌধুরী) ও অপেক্ষাকৃত সত্ প্রশাসকেরা ও পরিকল্পনা কমিশনের শিল্প খাতের দায়িত্বপ্রাপ্ত রেহমান সোবহান প্রমুখেরা কোনো কোনো কারখানার উন্নয়নে চেষ্টা চালাতে থাকেন। তার বিবরণ অধ্যাপক সোবহানের স্মৃতিকথায় বর্ণিত আছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের প্রচেষ্টা সফল হওয়ার আগেই ১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে হত্যাকাণ্ডে অর্থনীতির গতিমুখ পালটে দেয়।
পরবর্তীকালে অবাধ প্রতিযোগিতার লাইনে চলে যাওয়া হয়। বিশ্বব্যাংক, আইএমএফ রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের জন্য পরামর্শ দেয়। তারা বলতে থাকে, স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির দিকে যে যাত্রা শুরু করেছিল তা ভুল ছিল। খন্দকার মোস্তাকের আমলেই রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তর কার্যক্রম শুরু হয়। বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ বলতে থাকে রাষ্ট্রের হাতে কোনো ব্যবসায়-বাণিজ্য থাকতে পারবে না। জিয়াউর রহমান প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর তিনি ‘লাভজনক প্রতিষ্ঠানগুলো’ অন্তত ব্যক্তি মালিকানায় হস্তান্তরের ব্যাপারে আপত্তি জানান। এ নিয়ে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফের সঙ্গে জিয়াউর রহমানের এক ধরনের দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল।
এছাড়া কৃষি খাতের ওপর থেকে ভর্তুকি সম্পূর্ণ প্রত্যাহারের কথা বলা হয়। জিয়াউর রহমান এ ক্ষেত্রে একটু ধীরে এগোনোর পক্ষপাতী ছিলেন। এ ক্ষেত্রেও আমরা বলতে পারি—জিয়াউর রহমানকে রাষ্ট্র ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া না হলে বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শ অনুসারে অবাধ পুঁজিবাদি অর্থনীতি তাত্ক্ষণিকভাবে চালু করা সম্ভব হতো না। কিন্তু পরবর্তীকালে প্রেসিডেন্ট এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণের পর ঢালাওভাবে বিরাষ্ট্রীয়করণ কার্যক্রম শুরু করা হয়। এমনকি আওয়ামী লীগও ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া চালু রাখে। পরবর্তী সময়ে কোনো সরকারই বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেনি।
বর্তমানে আমরা যে স্বজনতোষণমূলক কতিপয়তন্ত্রের পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছি তাতে বৈষম্য এক ধরনের কাঠামোগত প্রবণতায় পরিণত হয়েছে। আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সংখ্যাগরিষ্ঠ শোষিতদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ছাড়া এ থেকে সহজে কোনো মুক্তির রাস্তা খোলা নেই। তবে শুরু করতে হবে গণতন্ত্রের রোডম্যাপ ও আশু সংস্কারের রূপরেখা ঘোষণার মাধ্যমে, যাতে শোষিতরা তাদের ইচ্ছামতো ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন।
লেখক: বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
সূত্র : ইত্তেফাক