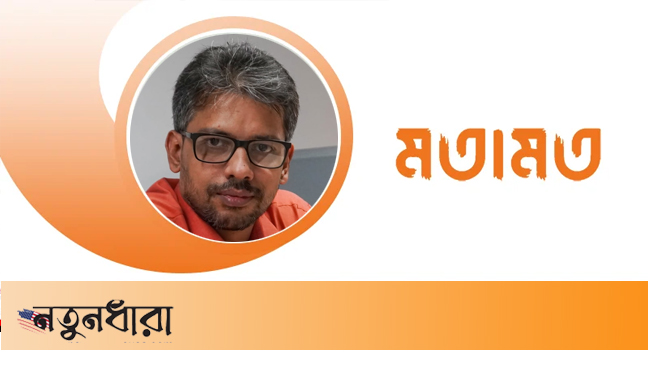
জানি না, বাংলাদেশে গণতন্ত্রের পথ আর কত কণ্টকাকীর্ণ হবে! গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী সময়ে আমরা নির্বাচনি গণতন্ত্রের একটা যথাযথ মডেল এই বাংলাদেশে দেখতে চেয়েছিলাম, যেটা বিগত সময়ের চেয়ে একদমই আলাদা হবে। মোদ্দাকথা, আওয়ামী আমলে যে মডেল দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশের ভোট-গণতন্ত্রের সেটার পুনরাবৃত্তি আমরা চাইনি। সেটার একটা আদর্শ মঞ্চ হিসেবে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য জায়গা থেকেই এই ভোট-গণতন্ত্র শুরু হয়েছে—বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।
দীর্ঘ অপেক্ষার পর এই নির্বাচনগুলো বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত আশা জাগানিয়া হয়ে উঠেছে। অথচ, দীর্ঘকাল এগুলো বন্ধ ছিল সরকার ও প্রশাসনের সদিচ্ছার অভাবে এবং নির্বাচন দিলে ‘ক্যাম্পাসে লাশ পড়বে’ অজুহাতে। ইতিমধ্যেই ২০২৫ সালের ডাকসু নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। ২০১৯ সালেও ডাকসু নির্বাচন হয়েছে। ৩৩ বছর পর জাকসুও নানা বিতর্কের মধ্য দিয়ে শেষ হলো। কোনো নির্বাচনেই তথাকথিত ‘লাশ পড়ার’ জুজু সত্য হয়নি। কিন্তু, নির্বাচনি অব্যবস্থাপনা ও কারচুপির অভিযোগ থেকে ডাকসুর ৬ বছরের ব্যবধানে হওয়া দুটি নির্বাচনকে যেমন রক্ষা করা যায়নি, জাকসুকেও গেল না। উপরন্তু, জাকসুর পিঠে কলঙ্কের দাগ হিসেবে যুক্ত হলো নির্বাচনি দায়িত্ব পালনকালে একজন তরুণ শিক্ষকের মৃত্যু।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (ডাকসু) নির্বাচন নিয়ে নানা প্রশ্ন এখনও উত্থাপিত হচ্ছে। তবে, ডাকসুর ‘রেকর্ড’কে কয়েকগুণ ছাপিয়ে গেছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। জাকসুতে যা হয়েছে, সেই তুলনা করলে, ডাকসু নির্বাচনকে অপেক্ষাকৃত অনেক ঝঞ্ঝামুক্ত বললে অত্যুক্তি হবে না।
২.
জাকসু নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ভোটের দিন তো বটেই, ভোটের আগের এবং পরের ঘটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশনের সুষ্ঠু নির্বাচন আয়োজনের প্রতিশ্রুতিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। অথবা, বলা যেতে পারে, নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হোক, সেটা আক্ষরিক অর্থেই আন্তরিকতার সঙ্গে তারা চায়নি। ডাকসুতে কোনো প্যানেলই অন্তত নির্বাচন বয়কট করেনি। কিন্তু, জাকসুতে আটটি প্যানেলের মধ্যে ছাত্রদল সমর্থিত একটি ও ছাত্র ইউনিয়ন সমর্থিত দুটি প্যানেলসহ প্রগতিশীলদের চারটি প্যানেল (মোট পাঁচটি প্যানেল) এবং উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বতন্ত্র প্রার্থী শেষ পর্যন্ত নির্বাচনে নানা অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনার অভিযোগ এনে নির্বাচন বর্জন বা বয়কট করেছে। এই প্যানেলগুলো পুনঃনির্বাচনেরও দাবি জানিয়েছে।
তবে, নির্বাচন বয়কটের প্রতিবাদে সাধারণ ছাত্রবেশে একজন সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে বক্তব্য দেন। পরে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় যে, তিনি আসলে সাধারণ ছাত্র নন, আদতে শিবিরকর্মী। সংবাদমাধ্যমও জেনে বা না-জেনে তাকে ‘সাধারণ শিক্ষার্থী’ হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেয়। আদতে, পুরো নির্বাচন ঘিরে জাহাঙ্গীরনগরে কর্মরত কিছু সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি ও স্থানীয় সাংবাদিক-নেতাদের আরও দায়িত্বশীল আচরণ প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু, তারাও নানান সংবাদ অতিরঞ্জিত করে প্রকাশ করেছেন, কখনও সংবাদমাধ্যমে, কখনও নিজেদের ব্যক্তিগত অ্যাকাউন্ট থেকে, কখনওবা নিজেদের নিয়ন্ত্রিত ক্যাম্পাস-সংশ্লিষ্ট পেইজগুলো থেকে। এর ফলে, গুজব যেমন ছড়িয়েছে, উত্তেজনাও বেড়েছে।
অন্যদিকে, শিক্ষার্থীদের পাঁচটি প্যানেল নির্বাচন বয়কট করার আগেই, অনিয়মের অভিযোগ এনে নির্বাচনি দায়িত্বে থাকা বিএনপিপন্থী তিনজন শিক্ষক নির্বাচন বর্জন করেছেন। শেষপর্যন্ত এ নিয়ে নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে দুই নির্বাচন কমিশনার ও তিন কর্মকর্তা সরে দাঁড়িয়েছেন।
নানা নাটকীয়তার পর ১১ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত ভোটের ফল ঘোষিত হয়েছে ১৩ সেপ্টেম্বর। ভাবা যায়! যে তিনটি প্যানেল নির্বাচন বর্জন করেনি, তাদের প্রার্থীরাই বিজয়ী হয়েছেন। তবে, ডাকসুর মতো জাকসুতেও ইতিহাসে প্রথমবারের মতো বড় বিজয় হয়েছে ছাত্রশিবিরের। জাকসুতে অবশ্য সহ-সভাপতি পদটি তারা জিততে পারেননি, জিতেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন প্যানেলের আব্দুর রশিদ জিতু। তবে, বিজয়ী ও বর্জনকারী যুযুধান প্রায় সবপক্ষই নির্বাচন ঘিরে নিজেদের অসন্তোষ ও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।
যার অর্থ হলো, আমরা সত্যিকার অর্থেই বাংলাদেশে একটা যথাযথ নির্বাচনি গণতন্ত্রের মডেল তৈরিতে ব্যর্থ হয়েছি আমরা। এত কেচ্ছাচার শুধু একটি প্রশ্নই সামনে আনছে: আমরা কি এমন জাকসু নির্বাচন চেয়েছিলাম?
৩.
বাংলাদেশের নির্বাচনি সংস্কৃতিতে ভোটের ফলাফল না-মেনে নেওয়ার একটি প্রথা বরাবরই ছিল। এমনকি বিজিত পক্ষ বিজয়ী পক্ষকে অভিনন্দন জানাতেও কার্পণ্যবোধ করে। সেই সংস্কৃতির বদল গণ-অভ্যুত্থানের পর এবারও হলো না। আবার, ‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে’র যে কৌশলও সেটিরও বিলোপ হলো না। আগে হওয়া ডাকসুর অভিজ্ঞতা থেকে জাকসু ঘিরে তাই প্রার্থী ও ভোটাররা স্বভাবতই অনেক বেশি সতর্ক ছিলেন বলা যায়। কিন্তু, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন ও জাকসু নির্বাচন কমিশন সেসব জানা সত্ত্বেও নিজেরা সতর্ক হননি।
হয়তো তারা সেটাই চেয়েছিলেন। নইলে ডাকসু নির্বাচনের মাত্র ২ দিন বিরতিতে তারা জাকসু নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ করেন কোন যুক্তিতে? সেটা কি এজন্য যে, যখন সারাদেশ ও মিডিয়া ডাকসু নিয়ে স্বাভাবিক ‘ওভার হাইপে’ থাকবে, তখন এর ছায়াতলে থেকে তারা সমস্ত নকশা বাস্তবায়ন করে ফেলবেন! অথচ, ৩৩ বছর পরে একটি নির্বাচন আয়োজন যারা করেন, স্বভাবতই তারা চাইবেন, তাদের কৃতিত্ব ফলাও করে মিডিয়ায় প্রচারিত হোক।
সত্য এই যে, ডাকসুর কারণে জাকসুর স্থান মিডিয়াতে অনেক সংকুচিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, ১৫ দিন ব্যবধান রাখলে সেটা হওয়ার প্রশ্নই ছিল না। বরং, জাকসু নিয়েও মিডিয়াতে, ডাকসুর মতো না হলেও, কাছাকাছি পর্যায়ের প্রচার-প্রচারণা ও স্থানসংকুলান হতো। অধিকন্তু, মরার উপর খাঁড়ার ঘা হিসেবে যেসব আচরণবিধি নির্বাচন কমিশন ধার্য করে, তা পুরোদস্তুর একটা নির্বাচনের আমেজকেই নষ্ট করে ফেলে। হলফ করে বলা যায়, এমন আচরণবিধি ডাকসুতে থাকলে, ডাকসু নির্বাচন ঘিরেও এমন ম্যারম্যারে আবহাওয়ার কথাই প্রচার ও প্রকাশ করতে হতো সংবাদমাধ্যমকে।
জাকসু এমন প্রচারবিমুখ হোক, এটা প্রশাসনের গভীর অন্দরের চাওয়া অনুযায়ীই হয়তো হয়েছে। তাতে যারা অনলাইন ও গোপন প্রচারণায় সিদ্ধহস্ত, তাদেরকে একটা অলিখিত সুবিধা দেওয়া গেছে। বাকিরা পিছিয়ে গেছেন, কেননা সংবাদমাধ্যমের ডাকসুকেন্দ্রিক ব্যস্ততার দরুণ তাদের পক্ষে জাকসুর প্রার্থীদের এতটা প্রচারের আলো দেওয়া সম্ভব হয়নি। জাবি প্রশাসনের এসব আকাঙ্ক্ষা পূরণ হলেও, ফাইনাল পরীক্ষার দিন মিডিয়ার কাছে তাদের সমস্ত অপেশাদার কর্মকাণ্ডকে তারা আর গোপন রাখতে পারেনি। নির্বাচনের দিন থেকে ফল ঘোষণা পর্যন্ত তিনদিন ঢাকার মিডিয়াপাড়ার কেন্দ্রস্থলগুলোর কাছে জাকসুই ছিল প্রধান মনোযোগ ও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। তাই এতসব অসঙ্গতি ধরা পড়ে গেছে।
সঙ্গে এটাও মনে রাখতে হবে যে, জাকসু নির্বাচন হলো ৩৩ বছর পরে। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এই পর্যন্ত ৫৩টি ব্যাচ অধ্যয়ন করেছে বা করছে। ১৯৯২ সালে আসা ব্যাচ থেকে ২০২৫ সাল পর্যন্ত মোট ২৬টি ব্যাচ বেরিয়ে গেছে, যারা জাকসু ভোটের স্বাদই পায়নি। এই ব্যাচগুলো থেকে যারা বিশ্ববিদ্যালয়টির শিক্ষক হয়েছেন, যাদের একটি বড় অংশ অধ্যাপকও হয়ে গেছেন, তাদের কারোরই শিক্ষার্থী হিসেবে জাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা নেই। এই শিক্ষকদের মধ্য থেকে যারা আবার একদমই সাম্প্রতিককালের গ্র্যাজুয়েট থেকে শিক্ষকতায় এসেছেন, জুনিয়র হবার কারণে তাদের ওপর দিয়েই গেছে সবচেয়ে বড় ধকল।
অভিযোগ উঠেছে, এই ধকলেরই বলি হয়ে প্রাণ দিয়েছেন চারুকলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও জাকসুর পোলিং কর্মকর্তা জান্নাতুল ফেরদৌস মৌমিতা (৩১)। একে তো ক্লাস-পরীক্ষার পাশাপাশি নির্বাচনি দায়িত্বের কারণে গত কয়েকমাসের অক্লান্ত পরিশ্রম, তার ওপর নির্বাচনি অব্যবস্থাপনা ও শেষ মুহূর্তের নানা অকার্যকর সিদ্ধান্তের কারণে শরীরের ওপর অমানুষিক অত্যাচার, প্রাণ কত সইবে! প্রায় বারো হাজার ভোটারের জন্য পুরো নির্বাচনজুড়ে কাজ করেছেন ছয়শতাধিক শিক্ষকের মধ্যে মাত্র ৬০-৭০ জন শিক্ষক, মানে প্রতি ২০০ ভোটারের জন্য একজন করে, যা এক অসম্ভবকে সম্ভব করতে চাওয়ার অমানবিক-পদ্ধতি ছাড়া আর কিছুই না! অথচ, লোকবল বাড়ানোর দাবি থাকলেও, প্রশাসন সেদিকে কর্ণপাত করেনি।
কেন্দ্রীয় ও হল সংসদ মিলে মোট ব্যালট পেপার ৫টি। সেগুলোর প্রতিটিতে সিলমোহর ও স্বাক্ষর করতে হয়েছে। ২০০ জনের হিসাবে একহাজার করে সিলমোহর ও স্বাক্ষর। তারপর আছে বিনিদ্র রজনীর শরীর। আপনি একজন মানুষকে যন্ত্র ভাবলে আর প্রভু সেজে ভৃত্য বা দাসানুদাস মনে করলেই কেবল একজনকে এমন পরিস্থিতিতে স্বাভাবিক রাখতে পারবেন। এই ক্যাম্পাসে জুনিয়রদের ওপর সিনিয়রদের মাস্তানি ও মর্যাদাহানি শিক্ষার্থী জীবনে আমরা এন্তার দেখেছি। কিন্তু, শিক্ষক জীবনেও এই সংস্কৃতি রয়ে যাবে তাই বলে!
অথচ, এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৯২ সালে হওয়া সর্বশেষ ও তার আগের জাকসু নির্বাচনগুলো শিক্ষক বা শিক্ষার্থী হিসেবে দেখার অভিজ্ঞতা আছে, এমন অন্তত ১২-১৩টি ব্যাচের বহু শিক্ষক আছেন, যারা সবাই এখন অধ্যাপক। অভিজ্ঞতার একটা জরুরি গুরুত্ব আছে। অভিজ্ঞতা না-থাকলে অপেশাদারিত্বও তৈরি হয়। আমার প্রশ্ন হলো, বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এই অধ্যাপকদের অভিজ্ঞতা ও সহায়তা নিতে চেয়েছিল কি? মৌমিতার এই মৃত্যু বিতর্কিত এই জাকসু নির্বাচনের গায়ে সবচেয়ে বড় কলঙ্কতিলক হয়ে থাকবে। তার এই অকাল অস্তযাত্রার দায় তাই প্রশাসন কোনোভাবেই এড়াতে পারে না।
৪.
এই নির্বাচন ঘিরে যত বিতর্ক, তার পরিষ্কার তিনটি ভাগ—নির্বাচন-পূর্ব, নির্বাচন-কালীন ও নির্বাচন-উত্তর।
নির্বাচনের তফশিল কয়েকবার পেছানোয় ২০১৩ সালে স্থগিত জাকসুর অভিজ্ঞতার কারণে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। তাছাড়া উপাচার্যের নিজেরও অনিচ্ছা প্রকাশ পায় ‘লাশ পড়বে’ মর্মে তার এক মন্তব্যের কারণে। তবে, শেষমেশ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারিত হওয়ায় সে শঙ্কা কেটে যায়।
নির্বাচন-পূর্ব সময়ে সবচেয়ে বড় বিতর্কটি ছিল অনিবার্যভাবেই সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেলের সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী অমর্ত্য রায়ের প্রার্থিতা বাতিলকে কেন্দ্র করে। তাকে ‘অনিয়মিত শিক্ষার্থী’ তকমা দেয় নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের মাত্র চারদিন আগে। ২৯ অগাস্ট চূড়ান্ত ভোটার ও প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হয়ে গেছে বলে এক রিটের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রার্থিতা হাইকোর্ট ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু, ব্যালট পেপার ছাপানো হয়ে গেছে, এমন অসত্য তথ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উচ্চ আদালত থেকে হাইকোর্টের রুলের ওপর স্থগিতাদেশ নিয়ে আসে। অথচ, যেদিন উচ্চ আদালতের চেম্বার জজ হাইকের্টের রুল স্থগিত করেন, সেদিনই (৯ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, ব্যালট পেপার ছাপা হবে নির্বাচনের দিন সকালে।
এই দ্বিচারিতা নির্বাচনকে বিতর্কিত করার জন্য যথেষ্ট। কিন্তু, প্রশাসনের ভাণ্ডারে যে বিতর্কের আরও রসদ ছিল, তা কে জানত!
৯ সেপ্টেম্বর ছিল প্রার্থীদের ‘ডোপ টেস্টে’র অদ্ভুত ও নিন্দনীয় এক কর্মসূচি। কিন্তু, সেই ডোপ টেস্টে সব প্রার্থী অংশ নেননি। কেন নেননি, তা প্রশাসন ভালো জানে। সেই ডোপ টেস্টের ফলও ঘোষণা করা হয়নি। ব্যালট যদি ছাপা হয়েই যায়, তাহলে ৯ সেপ্টেম্বর ডোপ টেস্ট করানোর যুক্তি কী? এর ফল যদি কোনো প্রার্থীর বিপক্ষে যেত, তাকে তো বাদ দেওয়া হতো। তাহলে, ব্যালট আবার ছাপানো হতো? এই যুক্তিতেও অর্মত্য রায়ের বিপক্ষে উচ্চ আদালতে বিশ্ববিদ্যালয় যা বলেছে, তা খাটে না। আর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা হয়ে যাবার পরে, এসব নাটকীয় বন্দোবস্ত অবিমৃশ্যতা নাকি ইচ্ছাকৃত, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়।
নির্বাচন নিয়ে অব্যবস্থাপনা কী পর্যায়ের ছিল, তার বড় একটি উদাহরণ পোলিং এজেন্ট থাকা না-থাকার প্রশ্নটি। আগের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে প্রশাসন ভোট গ্রহণের মাত্র সাত ঘণ্টা আগে, দিবাগত রাত ২টায় জানায় যে, পোলিং এজেন্ট রাখা যাবে। এই তথ্য অনেক নির্বাচনি কর্মকর্তা জানতেন না। অনেক প্রার্থী শেষ মুহূর্তে পোলিং এজেন্টের ব্যবস্থা করতে পারেননি। কেউ কেউ পারলেও, সব হলে পারেননি। আবার যাদের পোলিং এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিয়েছিলেন প্রার্থীরা, তাদের অনেককেই ছবি না থাকায় ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। পোলিং এজেন্টের অনুপস্থিতিতেই ভোট গ্রহণ শুরু করে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ‘আমাদের ওপর ভরসা রাখুন’! পোলিং এজেন্টের বদলে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন জায়গায় এলইডি স্ক্রিনে ভোট গ্রহণের প্রক্রিয়া সরাসরি দেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েও সেটির ব্যত্যয় ঘটিয়েছে প্রশাসন।
কাদের সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার জন্য এমন ভয়ানক বাজে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল প্রশাসন, তার তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। আদতে, পুরো জাকসু নির্বাচন নিয়েই একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া উচিত। কেন? সেটারই ইতিবৃত্ত এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন।
৫.
অনেক প্রাক্তনকে ভোটের আগের রাতে ক্যাম্পাসে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের সঙ্গে প্রশাসনের কর্তাব্যক্তিরা বৈঠকও করেছেন। এটা খোদ প্রশাসনের তরফেই নির্বাচনি আচরণবিধির লঙ্ঘন। এমনকি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন ফটকের বাইরে জামায়াতের বিভিন্ন স্তরের নেতাকর্মীদের অবস্থান করতে দেখা গেছে, যার ব্যাপারে প্রশাসন কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি।
খোদ ভোটের দিন বিভিন্ন সংগঠনের (ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, এনসিপি) বর্তমান পদাধিকারীরা (অছাত্র) বিভিন্ন হলের ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এছাড়া, শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার পেলেও, অন্যান্য প্রার্থীকে সে সুযোগ দেওয়া হয়নি। শিবিরের সমর্থকরা ভোটের দিন বিভিন্ন হলের সামনে প্যানেলের লিফলেট বিতরণ করেছেন, যা আচরণবিধির সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।
ভোটার তালিকায় ভোটারদের কোনো ছবি ছিল না এবং ভোটারদের হাতে ব্যবহার করা হয়নি অমোচনীয় কালি (কোথাও ব্যবহৃত হয়েছে মার্কার!)। একাধিক ভোট বা একজনের ভোট আরেকজন দিয়ে দেওয়ার পথ এতে প্রশস্ত করে দেওয়া হয়েছে।
আশ্চর্যের বিষয়, ছাত্রদের একটি হল সংসদের ব্যালটে কার্যনির্বাহী সদস্যের তিনটি পদের মধ্যে নাম ছিল একজনের। বাকি দুই প্রার্থীর নাম হাতে লিখে সেখানে ভোট গ্রহণ করা হয়েছে।
আরেকটি ছাত্র হলে মোট ভোটার ২৯৯ জন, কিন্তু, ব্যালট পেপার গেছে ৪০০টি। অভিযোগ উঠেছে, একজন উপ-উপাচার্য পুরো জাকসু নির্বাচনের জন্য ১০ শতাংশ অতিরিক্ত ব্যালট পেপার ছাপাতে বলেছেন। এই অসঙ্গতি ধরা পড়ার পর, নির্বাচনি অফিসাররা ব্যালট পেপার ছিঁড়ে ফেলার প্রস্তাব দিয়ে দায়মুক্ত হতে চেয়েছেন। কী বিস্ময়কর ব্যাপার!
নির্বাচন চলাকালে ছাত্রদের একটি হলে ভোটাররা কারচুপির প্রতিবাদ করলে, একজন নির্বাচনি কর্মকর্তা বলেছেন, ‘ভোট চুরি করলে কী করবেন আপনি?’—তার এই বক্তব্যের ভিডিও স্যোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে।
অসঙ্গতি ধরা পড়ায় কয়েকটি হলে ভোট গ্রহণ বেশ লম্বা সময় স্থগিত রাখা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পরও ভোট গ্রহণ করা হয়েছে কয়েকটি হলে। একটি হলের রিটার্নিং কর্মকর্তা সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ভোটাররা ৩০ মিনিট করে সময় নিচ্ছেন বলে সময় লাগছে। তার মানে, তাদের আগাম কোনো ধারণাই ছিল না যে, একজন ভোটারের কত সময় লাগতে পারে! কেন্দ্রীয় সংসদের ২৫টি ও হল সংসদের ১৩টি পদের ভোট সম্পন্ন করতে একজন ভোটারের বাস্তবিক অর্থেই এই সময় প্রয়োজন, যদি তিনি মুখস্থ না করে থাকেন কাকে ভোট দিতে চান। আর রিটার্নিং কর্মকর্তা নিজেদের দায় না দেখে, সরাসরি শিক্ষার্থীদের ওপর দোষ চাপিয়ে দিলেন। বুথ বাড়ানো উচিত ছিল—এই সত্যটুকুও স্বীকার করলেন না।
ছাত্রীদের হলে সংবাদমাধ্যমের প্রবেশাধিকার সংরক্ষিত হওয়ায় কয়েকটি হলে কারচুপি ও জাল ভোটের অভিযোগও উঠেছে। একটি হলের বুথের সামনে পড়ে থাকা ব্যালট পেপার উদ্ধার করেছেন পোলিং এজেন্টরা।
নির্বাচনকালীন এতসব অঘটনের পরও অসঙ্গতির কাণ্ডকারখানা চলমান ছিল নির্বাচন-উত্তরকালে।
ডাকসুর অভিজ্ঞতার কারণে অনেক প্রার্থী আগেই ভোট গণনার পদ্ধতি মেশিনের পাশাপাশি ম্যানুয়ালি করার দাবি জানান। ওএমরআর ব্যালট পেপার এবং কাউন্টিং মেশিন সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারীর জামায়াত-সংশ্লিষ্টতার কারণে প্রার্থীরা এমন দাবি করেন বলে জানা গেছে। কিন্তু, প্রশাসন এ ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করে। যার ফলে, ভোগান্তি হয় নির্বাচনি কর্মকর্তাদের। বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ২১টি হলের হাতে-মুখে ভোট গণনার পর্যাপ্ত স্থান না থাকার ফলে একটি একটি করে হলের ভোট গণনা করে ফল ঘোষণা করতে লেগে যায় রেকর্ড প্রায় ৪৮ ঘণ্টা। আর এই সময়ের মধ্যেই নির্বাচনে অনিয়মের অভিযোগ তুলে পদত্যাগ করেন দুই নির্বাচন কমিশনার।
এতসব অভিযোগের পরও, প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেছেন নির্বাচন নিয়ে কোনো অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি এবং নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। তার অধীনে একটি নির্বাচন বিশ্বস্ততা হারানোর পরও, তিনি এমন লজ্জাজনক বক্তব্য দিয়েছেন, যা আমাদের আওয়ামী লীগ আমলের জাতীয় নির্বাচন কমিশনারদের নির্জলা মিথ্যা কথাকে মনে করিয়ে দেয়। তাকে অন্তত একজন রেংলং খুমীর একটি ভোটের হিসেব দিতে হবে এখনই।
রেংলং জাকসুতে নির্বাচিত সকল প্রার্থীকে তার নিজের এবং জাবি আদিবাসী সংগঠনের পক্ষ থেকে অভিনন্দন জানিয়ে ফেইসবুকে পোস্ট দিয়েছেন। তবে অভিনন্দন জানানোর জন্য নয়, তিনি পোস্ট দিয়েছেন, তার একটি ভোটের হিসেব চেয়ে। মওলানা ভাসানী হল থেকে জাকসু নির্বাচনে সদস্য পদপ্রার্থী নিহ্লা অং মারমা একটি ভোটও পাননি। নিহ্লা জাকসু নির্বাচনে সম্প্রীতির ঐক্য প্যানেল থেকে কার্যকরী সদস্য পদে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাসানী হলে অনেক শিক্ষার্থী আছেন, যারা নিহ্লার বন্ধুবান্ধব, ঘনিষ্ঠ বয়োজ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ। আদিবাসী শিক্ষার্থীও অন্য হলের তুলনায় বেশি এই হলে। রেংলং লিখেছেন, “ধরে নিলাম প্রার্থীর বন্ধু-বান্ধব, জুনিয়র-সিনিয়র কেউ তাকে ভোট দেয়নি। এটাও ধরে নিচ্ছি আদিবাসী কমিউনিটির (এলোটেড হলের) কেউ তাকে ভোট দেয়নি। কিন্তু আমি একজন হলেও তাকে ভোট দিয়েছি, জেনেশুনেই সাবধানতায় ব্যালট পেপারে টিক (✅) চিহ্ন দিয়েছি যাতে ঘরের বাইরে দাগ পড়ে গিয়ে বাতিল না হয়ে যায়। ফলাফলে অন্তত শূন্যের জায়গায় এক (০১) হওয়ার কথা, কারণ আমি তাকেই ভোট দিয়েছি।”
৭.
৩৩ বছর পর যে জাকসু নির্বাচন হলো, তা নিয়ে বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষার্থীদের স্বাভাবিক এক উদ্দীপনা ও আগ্রহ ছিল। কিন্তু, এমন এক প্রশ্নবিদ্ধ নির্বাচন প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন ‘উপহার’ দিল, যা খোদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তিকেই প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এত অসঙ্গতি, অসংলগ্নতা, অব্যবস্থাপনা, অদক্ষতা ও অবিবেচনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে একটি নির্বাচনের জয়-পরাজয় হয়তো নির্ধারিত হলো। কিন্তু, তাতে গণতন্ত্রের প্রকৃত চেতনার জয় হয়নি। বরং, জাকসু নির্বাচনে এদেশের গণতন্ত্র আরও একবার তার প্রথাগত নির্বাচনি দুর্বৃত্তায়নের দুষ্টুচক্রে আবর্তিত হয়েছে বলেই প্রতীয়মান হলো।
প্রশাসনের কাছে বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আজীবনের নিবন্ধিত গ্র্যাজুয়েট হিসেবে আমার প্রশ্ন: সত্যই কি তারা এমন জাকসু নির্বাচনেরই নকশা করেছিলেন? আমরা কি এমন জাকসু নির্বাচন চেয়েছিলাম?
লেখক ও শিক্ষক। ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব জেনারেল এডুকেশনের সহকারী অধ্যাপক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর।
সূত্র: বিডিনিউজ ২৪.কম